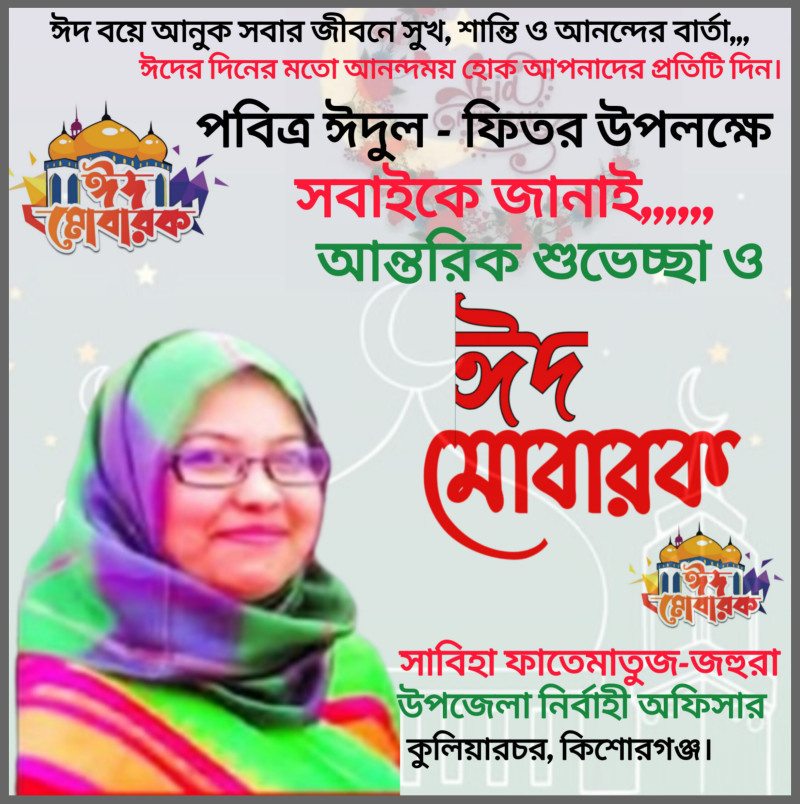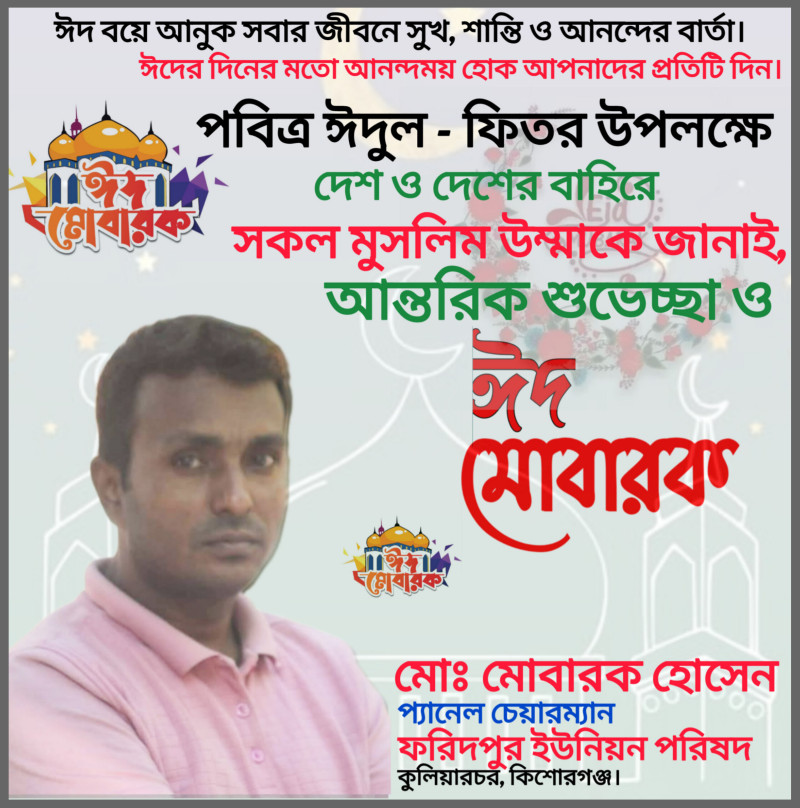মৃত্যু নয়, ভাইয়ের দীর্ঘজীবনের কামনা,ভাই ফোটার উৎসব।

রবিবার ভাইফোঁট॥ভাইফোঁটা সনাতন ধর্মের একটি উৎসব। এই উৎসবের নাম ভ্রাতৃদ্বিতীয়া অনুষ্ঠান। কার্তিক মাসের শুক্লাদ্বিতীয়া তিথিতে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। বাঙালি পঞ্জিকা অনুযায়ী, এই উৎসব কার্তিক মাসের শুক্লপক্ষের ২য় দিন উদযাপিত হয়। মাঝেমধ্যে এটি শুক্লপক্ষের ১ম দিনেও উদযাপিত হয়ে থাকে। এই উৎসবের আরও একটি নাম হল যমদ্বিতীয়া । কথিত আছে, এই দিন মৃত্যুর দেবতা যম তাঁর বোন যমুনার হাতে ফোঁটা নিয়েছিলেন। অন্য মতে, নরকাসুর নামে এক দৈত্যকে বধ করার পর যখন কৃষ্ণ তাঁর বোন সুভদ্রার কাছে আসেন, তখন সুভদ্রা তাঁর কপালে ফোঁটা দিয়ে তাঁকে মিষ্টি খেতে দেন। সেই থেকে ভাইফোঁটা উৎসবের প্রচলন হয়। ভাইফোঁটার দিন বোনেরা তাদের ভাইদের কপালে চন্দনের ফোঁটা পরিয়ে দিয়ে ছড়া কেটে বলে-
এইভাবে বোনেরা ভাইয়ের দীর্ঘজীবন কামনা করে। তারপর ভাইকে মিষ্টি খাওয়ায়। ভাইও বোনকে কিছু উপহার দেয়।অনেক সময় এই ছড়াটি বিভিন্ন পরিবারের রীতিনীতিভেদে পরিবর্তিত হয়ে থাকে। অতঃপর, বোন তার ভাইএর মাথায় ধান এবং দুর্বা ঘাসের শীষ রাখে। এই সময় শঙ্খ বাজানো হয় এবং হিন্দু নারীরা উলুধ্বনি করেন। এরপর বোন তার ভাইকে আশীর্বাদ করে থাকে (যদি বোন তার ভাইয়ের তুলনায় বড় হয় অন্যথায় বোন ভাইকে প্রণাম করে আর ভাই বোনকে আশীর্বাদ করে থাকে)। তারপর বোন ঐতিহ্যবাহী মিষ্টি দ্বারা ভাইকে মিষ্টিমুখ করায় এবং উপহার দিয়ে থাকে। ভাইও তার সাধ্যমত উক্ত বোনকে উপহার দিয়ে থাকে। ভাইফোঁটা একটি ঘরোয়া অনুষ্ঠান হলেও ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যে দিয়ে পালিত হয়। অনেক জায়গায় ভাইফোটা উপলক্ষে পারিবারিক সম্মেলনেরও আয়োজন করা হয়। কিন্তু এটা কি শুধুই একটা উৎসব, নাকি আছে অন্য কোনও ইতিহাস? খোঁজ করতে গিয়ে মিলে যায় এক সূত্র। চতুর্দশ শতাব্দীতে সর্বানন্দসুরী নামে এক আচার্য পণ্ডিতের তালপাতার পুথি, ‘দীপোৎসবকল্প’ থেকে জানা যায় জৈন ধর্মের অন্যতম মহাপ্রচারক মহাবীর বর্ধমানের মহাপ্রয়াণের পর তাঁর অন্যতম অনুগত সঙ্গী রাজা নন্দীবর্ধন মানসিক এবং শারীরিক ভাবে খুবই ভেঙে পড়েন। বন্ধ করে দেন খাওয়াদাওয়াও। এইরকম অবস্থায় তাঁর প্রিয় বোন অনসূয়া নন্দীবর্ধনকে তাঁর নিজের বাড়িতে নিয়ে যান। দিনটি ছিল কার্তিক মাসের শুক্ল পক্ষের দ্বিতীয়া তিথি। রাজার কপালে রাজতিলক পরিয়ে বোন অনসূয়া ভাইকে কিছু খাবার খাইয়ে দেন, আর বলেন, “রাজ্যের প্রজারা তোমার দিকে তাকিয়ে আছে, এই অনশন তোমাকে মানায় না। হে ভ্রাতা, হে রাজন, রাজতিলক এঁকে দিলাম তোমার কপালে এবং ক্ষুধা নিরসনের জন্য গ্রহণ করো খাদ্য। তুমি সাদর আপ্যায়িত হও। সর্ববিধ মঙ্গলের জন্য তুমি জেগে ওঠো, ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন। তোমার দীর্ঘায়ু কামনা করি। প্রতি বছর এইদিনে তোমাকে রাজতিলক পরিয়ে অভিষিক্ত করা হবে, এই আমার ব্রত।” এরপর বোনের দেওয়া খাবার খেয়ে এবং বোনের মুখে এই কথা শুনে রাজা নন্দীবর্ধন অনশন ভেঙে জীবনসত্যে উদ্ভাসিত হয়েছিলেন।‘দীপোৎসবকল্প’-এ বর্ণিত এই ইতিহাসের সেই সূত্র ধরে আমরা ‘ভাইফোঁটা’ উৎসবের সময়কাল আন্দাজ করতে পারি। মহাবীরের মহাপ্রয়াণ ঘটেছিল খ্রিস্টপূর্ব ৫২৭ অব্দে। সেই হিসেবে এই উৎসবের বয়স আড়াই হাজার বছর।
“যমুনা দেয় যমকে ফোঁটা
আমি দিই আমার ভাইকে ফোঁটা”
সেই কবে থেকে ভাইয়ের দীর্ঘায়ু কামনার ব্রতে জড়িয়ে যাচ্ছেন মৃত্যুদেবতা যম। যে যম আর মৃত্যু সমার্থক, সেই যম আর তার বোন যমুনার কথাই বোনা হয়ে যাচ্ছে “ভাই যেন মরে না”-র আকুতির আগে। এমন বিরোধাভাস কেন? কীভাবে বাংলার ভাইফোঁটার ছড়ায় জড়িয়ে গেলেন যম আর যমুনা? যমের অস্তিত্বও যেমন বেশ বিস্ময়ের। সূর্যের অপর নাম বিবস্বান। যম সূর্যপুত্র, তাই তিনি বৈবস্বত। যমের মা সংজ্ঞা। যমের স্পর্শে সংজ্ঞা চিরতরে লুপ্ত হয়, সূর্যের আলো মুছে যায় চোখ থেকে। অথচ, সেই সূর্য আর সংজ্ঞাই যমের পিতা-মাতা। পিতা-মাতার অস্তিত্বকেই যেন চ্যালেঞ্জ জানায় যমের অস্তিত্ব। ঋগ্বেদ অনুযায়ী, যমই প্রথম জন্মেছিলেন এবং প্রথম মৃত্যুবরণও করেছিলেন। জন্ম-মৃত্যুর অধীন বলে যমের দেবত্ব গোড়া থেকেই সংশয়ের। তিনি অজ বা শাশ্বত নন। ঋগ্বেদ অনুযায়ী তাঁর পরিচয় ‘মর্ত্য’। প্রথম মৃত হওয়ায় তিনি মৃত্যুপুরীর রাজা। কিন্তু দেবতা নন। আবার নেহাত মানুষও নন।‘যম’-কে নিয়ে তাই অস্বস্তি কাটে না সহজে। যম কি প্রশ্নাতীতভাবেই পুরুষ? ঋগ্বেদ অনুযায়ী, নিজেরই ভিতর থেকে যম মানববংশ সৃষ্টি করেছিলেন। জীববিশ্বের সাধারণ নিয়ম বেদ-পুরাণে অচল। কিন্তু সৃষ্টিতত্ত্বের ব্যাখ্যা আবার যুক্তিহীনও হতে চায় না। সূর্য আর সংজ্ঞার মিলনে যমের সঙ্গেই জন্ম যমীর। যম আর যমী মিলে কি অর্ধনারীশ্বর? তাই কি যম পারলেন নিজের ভিতর থেকেই মানববংশ সৃষ্টি করতে? আমাদের হয়তো মনে পড়ে যাবে, ‘যমজ’ শব্দটির মূলেও যম। আর, যমজ শব্দটি উভলিঙ্গবাচক।এরপর, বৈদিক যম আর যমী ক্রমে পরিণত হলেন পুরাণের যম আর যমুনায়। এই যমই ‘কাল’, কালের যমজ ‘কালিন্দী’। যম নীলাভ শ্যাম, যমুনার রঙও কালচে নীল। কালিন্দীর জলও কালো। যম মৃত্যুপুরীর রাজা, প্রথাগত দেবতা না হয়েও মৃত্যুর দেবতা আর যমুনা প্রেমপ্রবাহিণী। প্রেম আর মৃত্যু বারবার সমাপতিত আমিত্বের বিনাশে। মৃত্যুতে ‘আমি’-র অবসান। আর প্রেমের চিরকালীন চাওয়া-- ‘আরও প্রেমে আরও প্রেমে মোর আমি ডুবে যাক নেমে’। যম আর যমুনার সম্পর্কের অনুষঙ্গে স্থায়ী এই মৃত্যু আর প্রেম। অথচ ভাইফোঁটায় মৃত্যু নয়, ভাইয়ের দীর্ঘজীবনের আকাঙ্ক্ষা, প্রেম নয় নিষ্কাম স্নেহ। এবং সেই অনুষঙ্গেও চলে আসেন যম আর যমুনা। ভাতৃ দ্বিতীয়ায় বাংলার ঘরে ঘরে বোনেরা ভাইয়ের কপালে ফোঁটা দেয় তাদের স্মরণ করে। যে সম্পর্কের ভাষ্যে লেপ্টে মৃত্যু আর প্রেম, ভাইবোনের চেনা সম্পর্কের বাইরে বিপজ্জনক সব বাঁক যেখানে উপস্থিত, সেই যম-যমুনা বাংলার ভাইবোনের চেনা ঘরোয়া বয়ানে ঢুকে পড়েন দিব্বি। নাকি, তাদের একরকম জোর করেই জড়িয়ে নেওয়া হয়! আপাত বিপজ্জনক আখ্যানকে এভাবেই ভরে নেওয়া হয় সামাজিক নিয়মের চৌহদ্দিতে! যম-যমুনার বৈদিক আখ্যানকে ভুলিয়ে দিয়ে এরপর ক্রমশ স্থায়ী হয়ে উঠতে থাকে ভাইবোনের চেনা, নিটোল রূপকল্প। ‘কাঁটা যেন নড়ে না’-র আবেদনকে তাই কখনো-কখনো প্রতীকি নির্দেশ বলেও মনে হয়।অবশ্য এইসবই নিপাতনে সিদ্ধ কল্পনা মাত্র। কেন ও কীভাবে যম-যমুনা ভাইফোঁটার সঙ্গে মিলে গেলেন তারও পৌরাণিক ব্যাখ্যা দেখতে পাই। বলরামের সঙ্গে বিয়ে হল যমুনার। বিয়ের তিথি কার্তিক মাসের শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়া। বিয়ের আগে যমের কপালে ফোঁটা দিয়ে তার মঙ্গলকামনা করেছিলেন যমুনা। সেই সুতো ধরেই নাকি ভাইফোঁটার ছড়ায় আজো তারা ফিরে ফিরে আসছেন। এই ব্যাখ্যা বিশ্বাস করা-না করায় কিচ্ছু যায় আসে না ব্রতাচার কিংবা পুরাণের। যেভাবে যম-যমীর সম্পর্কের বৈদিক আখ্যানও সামান্য ব্যাঘাত ঘটায় না ভাইফোঁটার সময়। যম-যমুনা তাদের বৈদিক ও পৌরাণিক ইতিহাসের যাবতীয় রহস্যকে সরিয়ে রেখেই এসে বসেন ব্রতের ছড়ায়। মৃত্যুর দেবতা যমের দীর্ঘজীবন চেয়ে তাকে ফোঁটা দেন যমুনা। যমের অস্তিত্বের সঙ্গে লেপ্টে বৈপরীত্য, ভাইফোঁটার পাব্বনেও তার ব্যতিক্রম নেই। (সচ্চিদানন্দদেসদয়,সাংবাদিক)
আরও খবর


২৫ মিনিট আগে

১ ঘন্টা ১০ মিনিট আগে

১ ঘন্টা ৫৫ মিনিট আগে

১ ঘন্টা ৫৭ মিনিট আগে

২ ঘন্টা ১৩ মিনিট আগে

২ ঘন্টা ২৮ মিনিট আগে

২ ঘন্টা ২৯ মিনিট আগে